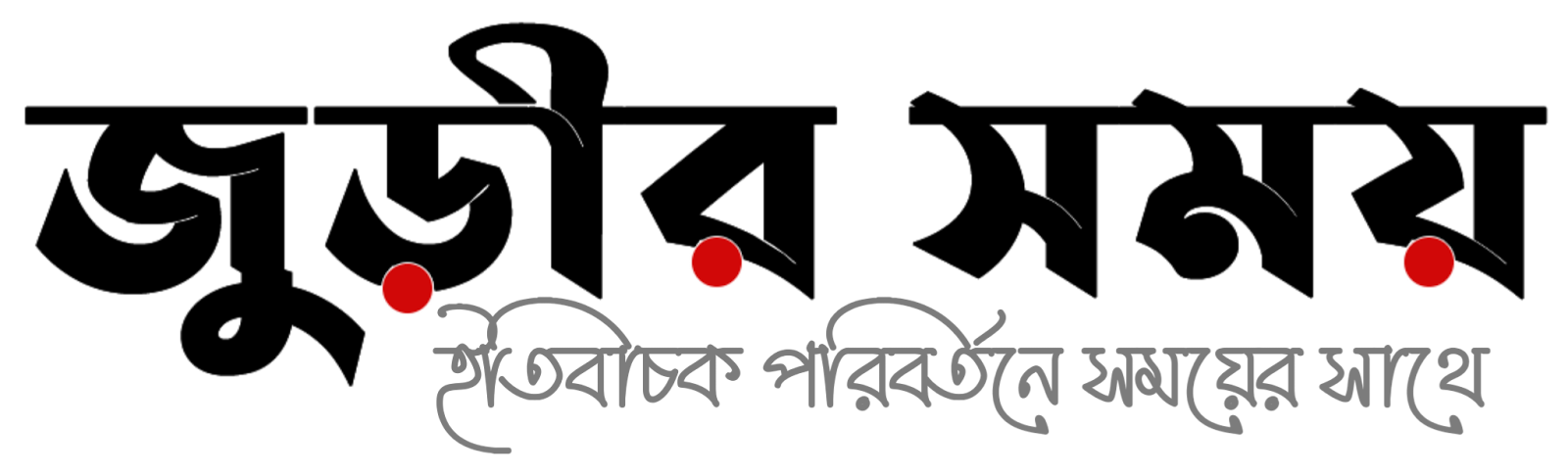খালেদ মাসুদ::
মানুষের কথার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। মানুষ তার মনের ভাব আকাঙ্খা প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। একে অপরের কাছে আসা,আলোচনা কিংবা ঝগড়া সবকিছুই প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। আমরা যেই মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি বা বলি সেটার মৌখিক রূপকে ভাষা বলা।
বাসা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার জন্য বিভিন্ন সময় অনেকগুলো আন্দোলন হয়েছে। সেই আন্দোলনে মানুষের রক্তের বিনিময়ে নিজের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। অনেকেই না জেনে বলেন যে, একমাত্র বাংলাদেশি বাঙ্গালিরাই ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। কথাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। ভাষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন হয়েছে। তবে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন হয়েছে বাংলাদেশ। একটা ভাষার মাধ্যমে একটা দেশের জন্ম হয়েছে। একটা জাতি নিজেদের আত্মপরিচয় পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে রেখেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘটিত হওয়া ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সমূহ হলোঃ
১.বাংলা (বাংলাদেশ): ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটি অংশে ছিল ১.পূর্ব পাকিস্তান ও ২.পশ্চিম পাকিস্তান।পাকিস্তানের মানুষ ছিল বাংলাভাষী। পাকিস্তানের কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে দেশের মানুষ। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। শহীদ রফিক জব্বার বরকত সালাম রক্তের বিনিময়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্ক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি দেয়।
২.মাদ্রাজ (ভারত): হিন্দিকে ১৯৬৫ সালে একমাত্র সরকারি ভাষা করা হয়। ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি তীব্র আন্দোলন শুরু হয়, দলে দলে মানুষ রাজপথে নেমে আসে। প্রায় দুইমাস ধরে সহিংসতা চলে দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে মাদ্রাজে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে হিন্দির সঙ্গে ইংরেজিকেও ব্যবহারিক সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।
৩.বাংলা (আসাম,ভারত): ভারতের আসামে বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ ১১ জনের মৃত্যুরহস্য উন্মোচনে ভারত সরকারের অনীহা একরকম গা-সওয়াই হয়ে গেছে আসামের বাঙালিদের।
৪.দক্ষিণ আফ্রিকা: দক্ষিণ আফ্রিকার ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল স্কুল পর্যায়ের ছাত্ররা। গাউটাংয়ের (তৎকালীন ট্রান্সভাল প্রদেশ) জোহানেসবার্গ শহরের সোয়েটোতে সংঘটিত আন্দোলনটি হয়েছিল ১৯৭৬ সালের ১৬ জুন । অঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ আফ্রিকানার ভাষায় (দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত শ্বেতাঙ্গ ডাচদের জার্মান-ডাচ ভাষার মিশ্রণ) শিক্ষাদান স্কুলে বাধ্যতামূলক করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। তারা তাদের মাতৃভাষা জুলু এবং ব্যবহারিক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ইংরেজিতে শিক্ষা নিতে বেশি আগ্রহী ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়। এ ঘটনাকে বলা হয় সুয়েটো অভ্যুত্থান। আর ট্র্যাজেডির দিনটিকে বলা হয় ‘ডে অব চাইল্ড’।
৫.আমেরিকা: ইউরোপ থেকে আসা উপনিবেশিকদের অত্যাচারে নেটিব আমেরিকানরা তাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল। গত শতকের ষাট-সত্তুরের দশকে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সময় এই নেটিভ আমেরিকান ভাষা রক্ষার দাবিও সামনে চলে আসে। মূল প্রস্তাবনার দীর্ঘ ২০ বছর আন্দোলন এবং আলোচনার পর ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নেটিভ/আদি/স্থানীয় ভাষা রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য একটি আইন পাস হয়।
৬.লাটভিয়া: রুশ ভাষাকে দ্বিতীয় দাপ্তরিক ভাষা স্বীকৃতি দিতে ২০১২ সালে গণভোট হয়।সেখানে লাটভিয়ানরা তা প্রত্যাখান করে।যদিও সোভিয়েত আমলে আমলে রুশ তাদের প্রধাণ ভাষা ছিলো।
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার জন্য মানুষ যে আন্দোলন করেছিল। তার মাধ্যমে সে তার মুখের ভাষা প্রতিষ্ঠিত করেনি বরং তার জাতির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছে।
লেখক: উপ-সাহিত্য সম্পাদক, জুড়ীর সময়
জুড়ীরসময়/ডেস্ক/জামান